জাতিসংঘের নির্দেশনায় প্রতি বছর ১৯ আগস্ট উদযাপন হয় বিশ্ব মানবতা দিবস। দিবসটির মাধ্যমে সারা বিশ্বের সাধারণ নাগরিকদের মানবিক কাজের প্রতি সমর্থন জোরদার করা যায়। এ বছর দিবসটি এমন এক সময়ে উদযাপিত হচ্ছে, যখন বাংলাদেশ এক গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী ক্রান্তিকাল পার করছে। আমাদের দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে লিখেছেন জেড আই খান পান্না
স্বাধীনতার ৫৩ বছরেও আমরা মানবাধিকারের বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে পারিনি। অনেকে নিজের অধিকার এখন ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন। হাসপাতালগুলোয় দালালে ভরা, স্কুল-কলেজে ভর্তি, সরকারি নথিপত্র বের করতে, পেনশনের টাকা তুলতেও দালাল। বিচার চাইতে গেলেও হয়রানির শেষ নেই। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতির পরিসংখ্যানগত পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যু, সীমান্তে হত্যা, সাংবাদিক নিপীড়নসহ মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বাধার মতো ঘটনার মধ্য দিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে চলেছে। জাতীয় পত্রিকাগুলোয় প্রকাশিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিবেদন বলছে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে অন্তত দু’জন নারীসহ আটজনের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে যশোরের অভয়নগর থানায় পুলিশ হেফাজতে আফরোজা বেগম নামে এক নারী মারা গেছেন। পরিবারের অভিযোগ, ঘুষের দাবিতে তাঁকে পুলিশ নির্যাতন করে হত্যা করেছে। আফরোজা বেগমের ছেলের অভিযোগ, পুলিশ তাঁর মাকে শারীরিক নির্যাতন করে। এ ছয় মাসে কারা হেফাজতে মারা গেছেন ৪৬ জন। এর মধ্যে কয়েদি ২০ জন এবং হাজতি ২৬ জন। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে সর্বোচ্চ ১৩ জন হাজতি এবং ১০ জন কয়েদির মৃত্যু হয়।
রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর মানুষের আস্থার জায়গা কমে গেলেই বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্যাতন অর্থাৎ নীতি পুলিশিং বেড়ে যায়। সেটিই হচ্ছে। এ ছয় মাসে দেশে গণপিটুনির ঘটনায় নিহত হন মোট ৩২ জন। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৬ জন। গত বছর এ সময়ে গণপিটুনির ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২৪।
আমাদের দেশে আইনত পুলিশ সদস্যরা কাউকে গ্রেপ্তার করে নির্যাতন করতে পারেন না। অথচ আমরা এমন অভিযোগ অহরহ পাচ্ছি। হেফাজতে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ২০১৩ সালে আইন হয়েছে। নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ অনুযায়ী, কেউ নির্যাতনের শিকার হলে আদালতে অভিযোগ করতে পারেন। শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন প্রমাণিত হলে শাস্তি হিসেবে ন্যূনতম ৫ বছরের কারাদণ্ড অথবা ৫০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। এ ছাড়া নির্যাতনের ফলে মৃত্যু হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড হতে পারে। এ আইন হওয়ার পেছনে মানবাধিকার সংস্থা, জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক মহলের একটা চাপ ছিল। এ আইনের আগে কেউ সাহস করত না পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করার। এখন মানুষ মামলা করার সাহস অন্তত পাচ্ছে। সভ্য জগতে এ আইন ভীষণ গুরুত্ব পায়। আমরা সে ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছি। আইনের বিধান আছে, অনেক মামলাও হয়েছে; কিন্তু বিচারের উদাহরণ খুবই নগণ্য। বাস্তবে দেখা গেছে, থানায় মামলাই নিতে চায় না। আদালতে মামলা করা হলে তা তদন্তের জন্য আবার ওই থানাতেই পাঠানো হয়। এ ক্ষেত্রে মামলা করার সাহস তো পাবে না সাধারণ মানুষ। আমরা এ বিষয়ে দাবি জানাচ্ছি, আক্রান্ত ব্যক্তি বা অভিযোগকারী ও তাঁর পরিবার ওই থানার বাইরে গিয়ে যেন মামলা করার অধিকার পান এবং এ মামলা চলার সময় ওই অভিযোগকারী ও তাঁর পরিবারকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সঙ্গে এসব মামলার তদন্ত আবার ওই থানার পুলিশ কর্মকর্তারাই করেন। এ ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা উচিত। এমনটা হলেও কিছুটা ইতিবাচক ফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।
নারীর প্রতি সহিংসতা–হয়রানি, ধর্ষণ, হত্যা, পারিবারিক নির্যাতনের চিত্র ভয়াবহ। এখনও রাস্তাঘাট ও কর্মক্ষেত্র কোথাও নারীর জন্য নিরাপদ নয়। লোকাল বাসে নারীর হয়রানির ঘটনা নিত্যদিনের। এ যেন সব সয়ে যাওয়া। এসব বদলানোর দায় নেই কারও। এসব সংকট জিইয়ে রাখা হয় কার স্বার্থে– সে প্রশ্নও তোলা যায় না। গণমাধ্যমও এখন সেটুকুই বলে যেটুকু বললে টিকে থাকা যায়। গত ছয় মাসে ১৪৫ জন সাংবাদিক বিভিন্নভাবে নির্যাতন, হয়রানি, হুমকি, মামলা ও পেশাগত কাজ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন।
ধর্ষণ বা সংঘবদ্ধ ধর্ষণ নিয়ন্ত্রণ না করতে পারাটা আসলে আমাদের আইন এবং বিচারব্যবস্থার দুর্বলতা। আইন ও বিচারব্যবস্থা যদি দ্রুত এটির সমাধান করত, তাহলে এমন অপরাধ করার আগে অনেকেই দশবার ভাবত। এমন অপরাধের শাস্তি আরও বেশি হওয়া দরকার। আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে দুর্বলতা, দীর্ঘসূত্রতা এবং গণসচেতনতার দুর্বলতা, নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণ, বাল্যবিয়ে বাড়াচ্ছে। এগুলো শুধু অপরাধ নয়; এখানে মানবিকতা বিদ্ধ হয়। কোনো সভ্য সমাজে এমন নিয়ন্ত্রণহীন নারী নির্যাতন চলতে পারে না। নারী নির্যাতন, ধর্ষণের বিরুদ্ধে টেলিভিশনে সচেতনতামূলক প্রচারণা থাকা উচিত। কিছু কিছু আছে। তবে যে পরিমাণে সচেতনতামূলক প্রচারণা থাকার কথা, তা নেই। গণসচেতনতামূলক প্রচারণা অনলাইন-অফলাইন সব মাধ্যমে বাড়াতে হবে। আমাদের সামাজিক সচেতনতাও কম। সামাজিকভাবে ধর্ষককে যতটা দোষী মনে করা হয়, তার চেয়ে ধর্ষণের শিকার মানুষটিকে বেশি অপরাধী মনে করা হয়।
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের বেলায় সমতলের সাঁওতাল, গারো, হাজং, খাসিয়া, মণিপুরি ও পটুয়াখালী-বরগুনার রাখাইন সম্প্রদায় প্রায় অবলুপ্তির পথে। যদিও এখানে জাতিগত দাঙ্গা নেই। তথাপি তাদের ভূ-সম্পত্তি ও সংস্কৃতির ওপরে নিবর্তনমূলক আচরণ লক্ষণীয় মাত্রায় বেড়ে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তির পরেও সেই চুক্তি বাস্তবায়নের দিক থেকে সরকারের কোনো রাজনৈতিক সদিচ্ছা পরিলক্ষিত হয়নি। এ কারণে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী এখনও ন্যূনতম মানবিক ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।
ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার আজও বন্ধ হয়নি। এই ধারাটির কারণে শুধু সন্দেহজনকভাবে নয়, তার সঙ্গে অজ্ঞাত হিসেবে বিভিন্ন মামলায় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ থেকে যায়। এই ধারাটি না থাকলে গুম, খুন এবং মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার মাত্রা অবশ্যই কমে যাবে। এই ধারায় যেমন সাধারণ মানুষ নিগৃহীত হয়, তেমন নিগৃহীত হয় রাজনৈতিক কর্মীরা। যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তখন সে এ আইনটিকে পুলিশের মাধ্যমে বিরোধী দলের নেতাকর্মীকে দমন-পীড়নের জন্যে অতি মাত্রায় উত্তম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। একই কথা বলা যায় রিমান্ডের ক্ষেত্রে। প্রতিটি জবানবন্দির আগে দেখতে পাই স্বীকারোক্তি প্রদানকারী রিমান্ড থেকে আসার পর স্বীকারোক্তি প্রদান করে। এ ব্যাপারে আপিল বিভাগের নির্দেশনাবলি আজও কার্যকর হয়নি।
বাংলাদেশের শ্রমিকদের জীবন ধারণের জন্যে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ হলেও যুক্তিসংগত হয়নি। একইভাবে প্রবাসী শ্রমিকদের বেলায়ও তাদের নিরাপত্তা, তত্ত্বাবধান এবং কোনো রকমের রাষ্ট্রীয় সুবিধা দেওয়ার উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি না। অথচ গার্মেন্ট শ্রমিক ও প্রবাসী শ্রমিক এরাই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়ার মূল দাবিদার।
সর্বশেষে বর্তমান প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাব, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীন ভূমিকা রাখার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।
জেড আই খান পান্না, চেয়ারপারসন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র(আসক)
প্রকাশিত লেখার লিঙ্কঃ মানবাধিকার কি ভাগ্যের হাতে!

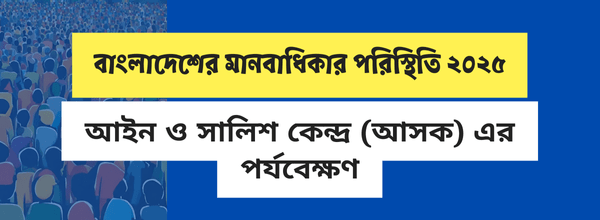










 Visit Today : 467
Visit Today : 467 Visit Yesterday : 772
Visit Yesterday : 772 Total Visit : 320003
Total Visit : 320003 Who's Online : 1
Who's Online : 1